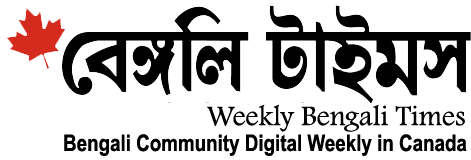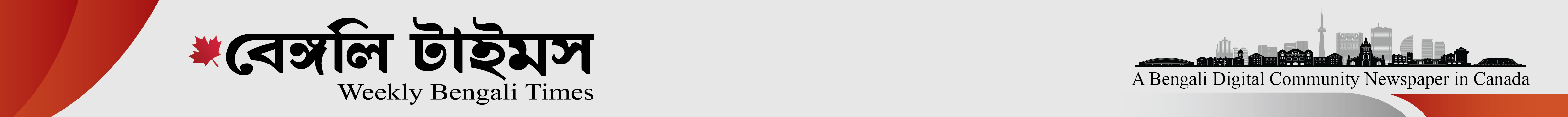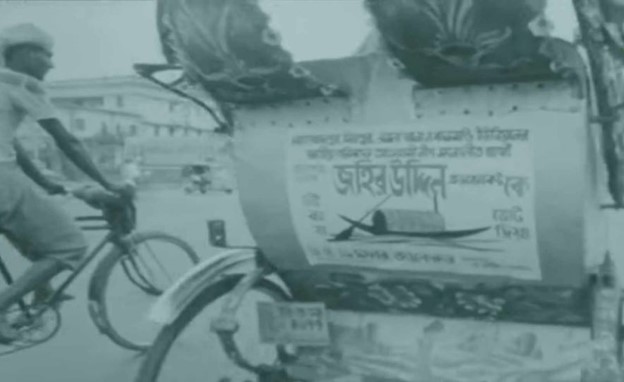
ঢাকার কাঁঠাল বাগানে ১৯৬৯ – ৭০ এর দিকে ছাত্রলীগের কোন শাখা ছিল না। সমস্ত পূর্ব পাকিস্তান তখন আন্দোলনের জোয়ারে ভাসছে আর এই আন্দোলনের মূল ভূমিকায় রয়েছে ছাত্রলীগ। তাই অল্প বয়সেই অবাক হলাম কাঁঠাল বাগানে কেন ছাত্রলীগের শাখা নেই। মাত্র কিছুদিন আগে আমরা ভুতের গলির ইউনুস চেয়ারম্যানের বাড়ি থেক কাঁঠাল বাগান গিয়েছি। লোকজন তেমন চিনতাম না। ক্লাস এইট কিংবা নাইনে পড়ি। শুধু জানতাম আমাদের বাসার উল্টো দিকে থাকতো আজিজ কাকা আর হাবিব কাকা। বলাকা সিনেমার সামনের গেট দিয়ে নিউমার্কেটে ঢুকতেই বড় দুটি কাপড়ের দোকান দেখা যেত ‘হাবিব ক্লথ স্টোর’ আর ‘আজিজ ক্লথ স্টোর’ এরা ছিল সেই আজিজ-হাবিব দুই ভাই। তাদের পাশেই ছিল আঁকশা (?) ফটোস্টুডিও এর মালিক খোকন ভাই, রতন ভাই, রানী আপা ঝর্না আপাদের বাসা। আর আমাদের গেটের ঠিক উল্টো দিকে থাকতেন ইপিএডিসি’র অফিসার মজিবুর রহমান খান (এম আর খান)। এক পর্যায়ে নিজ থেকে উদ্যোগ নিলাম কাঁঠাল বাগানে ছাত্রলীগের শাখা খোলার জন্য। কিন্তু এত ছোট ছিলাম যে ছাত্রলীগের সেন্ট্রাল কমিটির কাউকে চিনতাম না। মিজান ভাইকে বললাম মনের কথা। মিজান ভাই তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র (স্বাধীনতার পর তেজগাঁও কলেজের শিক্ষক হয়েছিলেন, গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইল)। মিজান ভাই কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া কিছু ছাত্র নিয়ে এলেন আমাদের দারোগা সাহেবের বাসায় (মহিউদ্দিন দারোগা বলে সকলে জানত)। তার ছেলের নাম ছিল ফাত্তা। স্বাধীনতার অনেক পরে ফাত্তা যখন বেশ বড়, তখন কারা যেন তাকে হত্যা করে রাস্তায় ফেলে রেখে যায়)।
ফেলু ভাই (আসল নাম মনে নেই) আর হাফিজ ভাই (সম্ভবত নামটি ছিল হাফিজ উদ্দিন) নামের বড় ভাইদের সাথে কথা হল। ফেলু ভাই থাকত কাঁঠাল বাগান তালতলা মাঠের পাশে দোতালা একটা বাড়িতে। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তাদের পাশেই ছিল একটা টিনের মেস। সেখানেই থাকতেন মিজান ভাই। হাফিজ ভাই থাকতেন রেল লাইনের কাছাকাছি কোথাও। দুই তিনদিন মিটিং হবার পর ঠিক হল সেন্ট্রাল কমিটি থেকে একজন ছাত্র নেতাকে নিয়ে এসে কাঁঠাল বাগান ছাত্রলীগ শাখার আনুষ্ঠানিক নাম ঘোষণা করা হবে। কাঁঠাল বাগানের বাজারের পাশে বড় গেটের একটা বাড়ি ছিল। সামনে ছিল লোহা-গ্রিল এর দোকান। সম্ভবত হোসেন আলী সাহেবের বাসা (নবাব আলী হোসেন আলী নাম খুব শুনেছি ছোট বেলায়)। যখন ঢাকার গ্রিন রোডর নাম ছিল ‘কুলীর রোড’ তখন কাঁঠাল বাগানকে ডাকা হত ‘হাসান ট্যাগ’ বা ‘হাসান-উদ্দিনের ট্যাগ’। নবাব আলী, হোসেন আলী নামের কয়েক ভাই ছিল খুব প্রতাপশালী। সেই হোসেন আলী সাহেবের বাড়ির লনের সবুজ ঘাসের ওপর আমরা কাঠের ফোল্ডিং চেয়ার বিছিয়ে বসলাম। আমাকে কাঁঠাল বাগান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হবে কিনা সেটা নিয়ে অনেকক্ষণ কথা হল। সভাপতি হাফিজ ভাই সহ তাতে কারো আপত্তি নেই কিন্তু আমার বয়স অল্প। সম্পূর্ণ উদ্যোগ আমার। তবুও ঐ বয়সের কাউকে কি সাধারণ সম্পাদক করা ঠিক হবে? এই নিয়ে চলল আলোচনা। শেষ পর্যন্ত হাফিজ ভাই সভাপতি, ফেলু ভাইকে সাধারণ সম্পাদক এবং আমাকে সহ-সাধারণ সম্পাদক করে কমিটির নাম ঘোষণা করা হল। সেই থেকে কাঁঠাল বাগান ছাত্রলীগ স্বাধীনতার সব আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল।
১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের সময়ও আমারা ছিলাম সক্রিয়। ইলেকশনের প্রস্তুতি পর্বে বঙ্গবন্ধুকে কাঁঠাল বাগান আনার কথা চিন্তা ভাবনা হল। আমার আব্বা সাখাওয়াৎ হোসেন ছিলেন ধানমন্ডি থানা আওয়ামীলীগ এবং স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি। বঙ্গবন্ধুর পাটগাতি-গেমাডাঙ্গা স্কুলের তিনি জুনিয়র ছাত্র। বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সাথে ছিল পারিবারিক বন্ধুত্ব এবং নিত্যদিনের আসা যাওয়া। কিছুদিন আগে আমার বড় বোনের বিয়েতে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে এসেছিলেন (বেগম মুজিব, শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, রাসেল ও কামাল ভাই)। বিয়েটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল অর্ধসমাপ্ত ধানমন্ডির ভুতের গলির কমিউনিটি সেন্টারে (ভুতের গলি মসজিদের ঠিক উল্টো দিকে)। এসমস্ত কথা অনেকেই জানতো। কাজেই কিছু লোক এসে আব্বাকে অনুরোধ করলেন বঙ্গবন্ধুকে কাঁঠাল বাগানে আনার ব্যাপারে সাহায্য করতে। বঙ্গবন্ধু সম্মতি দিলে শুরু হল প্রচার কাজ। তখন আমি ছিলাম স্লোগান মাষ্টার, মানে স্লোগান দিতে ওস্তাদ। ‘জয় বাংলা’ বলে চিৎকার দিলে গলাটা শেষের দিকে মেয়েদের মত চিকন সুরে বাজত। তাতে কি, স্লোগান দিতে পিছপা হতাম না। মিছিলের সামনে থেকেই স্লোগান দিতাম।
তালতলা মাঠে সত্যি সত্যি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আসা হল। জাতীয় পরিষদের আওয়ামীলীগের মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা করা হল সেখানে। মোহাম্মদপুর, মিরপুর, রমনা ও ধানমন্ডি ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন মোহাম্মদ জহিরউদ্দিন। তাকে সাথে নিয়ে এলেন বঙ্গবন্ধু। এই মিটিং এর বেশিরভাগ মাইকিং আমি আর হাফিজ ভাই করেছি। আমার হাতে মাইক এলেই বলতাম ‘ঐতিহাসিক তালতলা ময়দানে’…. এখন ভীষণ লজ্জা হয়, ঐতিহাসিক বটতলা শুনতে শুনতে মনে করতাম সব গাছ তলাই বুঝি ঐতিহাসিক, তাই কাঁঠাল বাগানের তালতলা মাঠকে বলতাম ঐতিহাসিক ময়দান। হাফিজ ভাই প্রথমদিকে কেন ভুলটা ধরিয়ে দিতেন না কে জানে। মঞ্চে ওঠার ছোট সিঁড়িতে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। যাবার সময় বঙ্গবন্ধু আমার ঘাড়ে হাত রেখা বাহবা দিলেন। আব্বা মনে করিয়ে দিলেন, এই যে বাবলু। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন ‘অনেক কাজ করতে হবে’।
ছোট বেলায় আব্বা আমাদের ভাইবোনদের রিক্সা বেবিট্যাক্সিতে ভরে ঈদের দিন নিয়ে যেতেন বঙ্গবন্ধুর বাসায়। ঈদের প্রথম সালাম তাকেই করতাম। তিনি যথারীতি মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করতেন। রান্নাঘর আর বারান্দার মাঝে একটা খাবার টেবিল ছিল সেখানে বসে সীমাই-জর্দা খেতাম। পেছনে ছিল গরু রাখার ঘর। কবুতর এবং হরিণ। উঁকি দিয়ে সেগুলো দেখতাম। আকরাম মামার (বঙ্গবন্ধুর শ্যালক) হাত ধরে ঘুরতাম। আম্মা চলে যেতেন উপরে। আমরাও সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করতাম। একবার কানাডা থেকে বাংলাদেশে যাবার পর দুই ছেলে আর স্ত্রীকে নিয়ে যখন বঙ্গবন্ধু যাদুঘরে যাই, সেই সিঁড়ি পতাকাতে ঢাকা দেখে পাগলের মত কেঁদে উঠেছিলাম। আমার ছোট্ট শিশু সন্তানটিও তার বাবার কান্না দেখে কেঁদে দিয়েছিল। আমার স্ত্রী তার স্বামীর কান্না দেখা কেঁদে দিল। সাথে ছিল মেরী খালাম্মা (আমার ছোট খালা)। বঙ্গবন্ধু তাঁকে তুই করে ডাকতেন। বুড়া বয়সে তিনি বললেন চল তোর সাথে ভাইজানের (বঙ্গবন্ধুর) বাসায় যাব। তিনিও দেয়াল ধরে কাঁদতে লাগলেন। অনেকে হয়তো মনে করছেন ব্যক্তিগত বন্ধনের কারণে আমরা কেঁদেছি। বিশ্বাস করেন সেদিন দেখলাম স্কুল কলেজের ইউনিফর্ম পরা প্রায় সব বাচ্চারাই কাঁদছে। পাকা দাড়িতেও একজনকে কাঁদতে দেখলাম। হয়তো এটা রোজকার দৃশ্য কিন্তু আমি সেই একবারই গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধু যাদুঘরে তাই এ দৃশ্য সব সময়কার দৃশ্য কিনা আমার পক্ষে বলা কঠিন।
যাইহোক যেহেতু জহিরউদ্দিন ছিল একজন উর্দুভাষী তাই অন্য স্থানে ভাষণ দেবার মত বঙ্গবন্ধু কাঁঠাল বাগান তাল তলা মাঠেও জোর দিয়ে বললেন ‘আমার উপর আপনাদের বিশ্বাস আছে? আমি যদি কলাগাছকেও দাঁড় করাই আপনার তাকেই ভোট দেবেন’? অবশ্যই জহিরউদ্দিন বিপুল ভোটে জিতেছিল। পরবর্তীতে এই জহিরউদ্দিন, পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজা ত্রিদিব রায়, ময়মনসিংহ এর নুরুল আমিন (এরা ছিল জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্য তবে জহিরউদ্দিনই একমাত্র আওয়ামীলীগের টিকিটে মনোনীত হয়েছিল) পাকিস্তানীদের পক্ষে যোগ দেয়। ১৯৭০ এর নির্বাচন এর কিছু আগে আমরা কাঁঠাল বাগান ছেড়ে চলে আসি ধানমন্ডির ক্রিসেন্ট রোডে। গলির মুখে দুটি বড় বিল্ডিং ছিল তার একটি ছিল পরিবার পরিকল্পনার অফিস। সম্ভবত অন্যটি আইডিএল স্কুল। পাশেই একটা খালি জায়গা তারপর কয়েকটা টিনের ঘর। আমরা তারই একটা টিনের ঘরে থাকতাম। আমাদের বাসা থেকে আর একটু সামনে ছিল চিত্রনায়িকা শাবানা ও চিত্রনায়ক আনোয়ার হোসেনের বাসা।
কাঁঠাল বাগান থাকা অবস্থায় একটি কাজের কথা মনে পড়ছে। নির্বাচনের মিছিল নিয়ে যাওয়া হবে তাই হোসেন আলী সাহেবের বাড়ির ভেতর বাঁশ মূলী চাটাই দিয়ে বানানো হল নৌকা। বানানোর সময় খেয়াল ছিল না যে নৌকা বিশাল বড় হয়ে যাচ্ছে। পরে সেটাকে আর ঠেলাগাড়িতে ওঠানো যাচ্ছিল না। শেষে বুদ্ধি করে দুটো ঠেলাগাড়ি জোরা দিয়ে তার উপর ওঠানো হল বিশাল আকৃতির নৌকা। সম্ভবত নির্বাচনের আগে এত বড় নৌকা আর কেউ দেখে নি তাই পরেরদিন পত্রিকায় সেটার ছবি ছাপানো হল। আর আমি যে কাজটা করলাম সেটা আরো মজার। কথাটি আগেও একবার লিখেছিলাম। নৌকা বানানোর সময়টাতে আমি ঘুরতে ঘুরতে আবিষ্কার করলাম মিউনিসিপালটির তিন চাকার ময়লা গাড়ীর পরিত্যক্ত ফ্রেম। ময়লা ফেলার যে জায়গাটা থাকার কথা ছিল সেটা ছিল না, মানে শুধু ফ্রেমটাই ছিল। সেটাকে উঠিয়ে আমি চালাতে লাগলাম। নবাব সিরাজউদ্দৌলা সিনেমা দেখার পর সব সময় মাথার মধ্যে কামানের একটা ছবি লেগে থাকতো। তিন চাকার বাহনকে মনে হল কামান-বাহী যান। পাশে ছিল একটা গ্রিলের দোকান। সেখান থেকে পরিত্যক্ত একটা মোটা পাইপ জোগাড় করে সেটাকে তিন চাকার উপর বসিয়ে কামান কামান করে ঘুরে বেড়ালাম। কিন্তু বড় আকারের পাইপ তাই চলার সময় ঘন ঘন পড়ে যাচ্ছিল। হোসেন আলী চাচা গ্রিল মিস্ত্রিকে বললেন পাইপটা ওয়েল্ডিং করে দিতে। ব্যাস, হয়ে গেল যুতসই কামান। কালো রঙ লাগিয়ে দিলাম পাইপটার উপর। তাতেই কামান হয়ে গেল চোখে পড়ার মত। তবু ৭০ এর কামান, কেন যে অপূর্ণ লাগছিল। আবার গেলাম গ্রিলের দোকানে। নিয়ে এলাম সিলভার কালার। কামানের এক দিকে লিখলাম ১১ দফা অন্যদিকে ৬ দফা। কাঁঠাল বাগান বা ধানমন্ডি থানা আওয়ামীলীগের মিছিল পূর্ণতা পেল। মিছিলের আগে কামান আর মধ্যমণি হল বিশাল নৌকা। জিপিও’র কাছে এলে কামানের মুখে একটা হাত বাজী রেখে ধরিয়ে দিলেম দিয়াশলাইয়ের কাঠি। বিকট শব্দ হল সাথে ধোয়া ছুটতে লাগল। কামানটা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হল। পরের দিন আমার হাতে লেখা ৬ দফা (কিংবা ১১ দফাও হতে পারে) কামানের ছবি ছাপা হল এক পত্রিকার পাতায়। কোন সাংবাদিক হয়তো যুদ্ধের গন্ধ পেয়েছিলেন তাই ছবিটি ছাপিয়ে দিয়েছিলেন পত্রিকার পাতায়। নিজের হাতের লেখা দৈনিক পত্রিকার পাতায় দেখে যে অনুভূতি হয়েছিল সে আর ভোলার নয়। এই ছবিটি চেয়ে অনুরোধ করেই আগে একটা লেখা লিখেছিলাম। এখনো তো অনেক ছবি অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে যদি ছবিটি দেখতে পেতাম তাতে মনটা জুড়িয়ে যেত।
যুদ্ধের আগে আমি গোপন সঙ্কেতের একটি ভাষা আবিষ্কার করে ফেললাম। বাংলা কথাগুলো অনেকটা জাপানি ভাষার মত করে লিখতাম। দেশের কথা, রেল লাইনের নিচে ডোবার পাশে গিয়ে কাঠের বন্দুক দিয়ে ট্রেনিং নেবার কথা এগুলো লিখতাম। ‘আরামে দাঁড়াও’ ‘সোজা হও’ বাংলায় এই সমস্ত আদেশ শুনতেই বাঙালি হবার গৌরব জেগে উঠত। ক্রিসেন্ট রোডের বাড়িতে থাকা অবস্থায় এলো ২৫শে মার্চ। ২৬ মার্চ দেখলাম মাথায় গুলি খাওয়া প্রথম মৃত দেহ। শাহজাহান নামের এক মাদ্রাসার ছাত্র আব্বার ব্যবহার করা সবুজ জিপ গাড়িটিতে রাতে ঘুমিয়ে পাহারা দিত। চাকরির খোঁজে সে এসেছিল নোয়াখালী থেকে। ২৫ মার্চ রাতের প্রচণ্ড গোলাগুলিতেও সে গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় নি। ২৬ মার্চ ফজরের আযান শুনে মসজিদের দিকে রওনা দিতেই তাঁকে ধাওয়া করে পাকিস্তান মিলিটারি। দেয়াল টপকিয়ে সামনের বাসা পার হয়ে আসতে চেয়েছিল হয়তো। কিন্তু দেয়ালে ওঠা অবস্থায় মাথায় গুলি খেয়ে পড়ে যায়। পাশের বাড়ির দেয়ালের ভেতর পড়ে ছিল তার লাশ। পরের দিন কার্ফু উঠিয়ে নিলে সেই জীপগাড়িতে শাহজাহানকে নিয়ে যায় আব্বা। আজিমপুর কবরস্থানে নেবার পথে জিপ থামিয়ে জনতা আরো কিছু লাশ উঠিয়ে দেয়। ঠিক মনে নেই আরো কি কি লেখা ছিল আমার একাত্তরের ডাইরিতে। একসময় কে যেন পাতাগুলো ছিঁড়ে চুলার আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছিল। কিন্তু তবুও একটা পাতা কি করে যেন বেঁচে যায়। সেই পাতাটির সাংকেতিক চিহ্ন পড়তে আমার নিজেরই এখন খুব কষ্ট হয়। আর ইংরেজিতে লেখা কিছু কোটেশন দেখে বোঝা যায় তখন কি ভাবনা খেলা করতো আমার মত তরুণদের মনে। দিনরাত্রি কী ভাবতাম আমরা। যেমন;
‘Two heads are better than one’
‘Slow and steady wins the race’
এখনো ৭১ এর পাতা শূন্য ডাইরি নিয়ে ঘুরে বেড়াই। শূন্য বলতে একদম শূন্য না, সাথে আছে একটি ছেড়া পাতা আর তাতে ৭১ লেখা।
স্কারবোরো, কানাডা