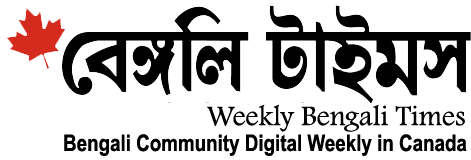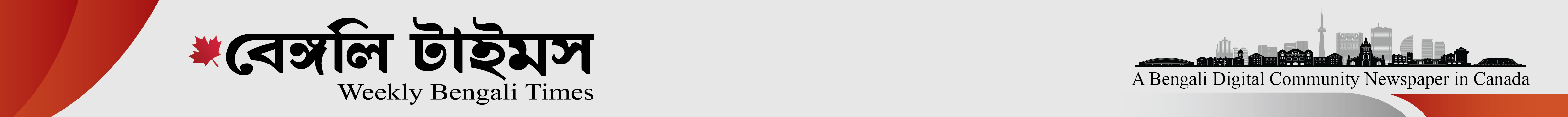ভিন্ন দেশ নিয়ে বাংলা ভাষায় লেখালেখির ক্ষেত্রে জাপান বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। প্রায় প্রতি বছরই বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলা থেকে জাপান বিষয়ে বই প্রকাশ রীতিমত দৃষ্টি কাড়ার মত ব্যাপার। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাপান যাত্রার পূর্বেও যেমন জাপান বিষয়ে অন্তত ৫টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় তেমনি ১৯১৯ সালে ‘জাপান-যাত্রী’ প্রকাশিত হওয়ার পরেও প্রবল সে ধারা অব্যাহত। জাপান বিষয়ে রচিত অধিকাংশ গ্রন্থই, স্বভাবসিদ্ধভাবে, ভ্রমণকাহিনীমূলক। জাপানের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি নিয়ে সত্যিকারভাবে রচিত গবেষণা গ্রন্থও একেবারে দুর্লভ নয়। বাংলাদেশের লেখক জাপান প্রবাসী গবেষক প্রবীর বিকাশ সরকারের ‘জানা-অজানা জাপান’ (দুই খণ্ড) রীতিমত চমক সৃষ্টিকারী এক প্রয়াস।
রবীন্দ্র-পূর্ববর্তীকালে জাপান নিয়ে লেখা প্রথম গ্রন্থ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৮২-?) ‘জাপান’ প্রকাশিত হয় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে। শিক্ষার্থে জাপান ভ্রমণ শেষে জাপান বিষয়ক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় না থাকার অনুভব থেকেই সুরেশচন্দ্রের এ গ্রন্থ রচনা। এতে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা যেমন পরিস্ফুটিত, তেমনি ২৫ বছর জাপানে বাস শেষে ইংরেজ লেখক আর্থার লয়েড লিখিত ‘এভরিডে জাপান’ গ্রন্থের প্রভাবও সুস্পষ্ট। সমসাময়িক জাপান নিয়ে অন্য যে আরেক লেখককে যথেষ্ট উৎসাহী দেখা যায় তিনি যশোরের মন্মথনাথ ঘোষ (১৮৮২- ১৯৪৪)। দুবার জাপান ভ্রমণ করলেও দ্বিতীয়বারের জন্য তাঁর ভ্রমণ ছিল দীর্ঘ বিরতি দিয়ে ১৯৩৩ সালে। প্রথমবার জাপানে শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর ভ্রমণ এবং সে প্রেক্ষাপটেই তিনি রচনা করেন মোট তিনটি গ্রন্থ যার মধ্যে তৃতীয়টি অর্থাৎ ‘সুপ্ত-জাপান’ প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে। অন্য দুটি গ্রন্থ ‘জাপান-প্রবাস’ ও ‘নব্যজাপান’ ১৯১০ সাল থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত তথ্য এই যে জাপান নিয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম এই দুইজন লেখকের দুজনেই ১৯০৬ সালে জাপানে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের গমনের কারণ ছিল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ। তবে মজার যে ১৯০৬ পূর্বকালে জাপানে বাঙালির গমন ও অবস্থান বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান এখনও শুরুই হয়নি।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাপান যাত্রার অব্যহিত পূর্বকালে জাপান বিষয়ে বাঙালি আর যে একজনের গ্রন্থ বর্তমানে সুলভ তিনি হরিপ্রভা তাকেদা। বাংলাদেশে অবস্থানরত জাপানি নাগরিককে বিয়ে করার কারণে ঢাকাবাসী ব্রাহ্ম এই নারী ১৯১২ সালের নভেম্বর জাপান যাত্রা করেন এবং চার মাস অবস্থান শেষে ফিরে যে গ্রন্থটি রচনা করেন তা ‘বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা’ শিরোনামে ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়। দুর্লভ সে গ্রন্থটির পুনঃপ্রকাশ ঘটেছে ১৯৯৯ সালে জাপান প্রবাসী বাংলাদেশি শিক্ষক মনজুরুল হকের উদ্যোগে।
রবীন্দ্রনাথের জাপান যাত্রার পূর্বেই জাপানি শিল্পী সাহিত্যিকদের শান্তিনিকেতনে আগমন সুর্যোদয়ের দেশটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট উৎসাহী করে তোলে। কয়েকবার উদ্যোগ গ্রহণ করার পর তাঁর সে উৎসাহ সফলতার মুখ দেখে ১৯১৬ সালে। এশিয়ার প্রথম নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের জাপান গমন দেশটির মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল অভূতপূর্ব আলোড়ন। যদিও সে উৎসাহে ভাটা পড়ে যায় দ্রুতই। জাপানের রাজনীতি বিশেষ করে রণনীতি বিষয়ে কবিগুরুর উন্মুক্ত বক্তৃতা জাপানিদেরকে প্রাচ্য এ দার্শনিকের নিকট থেকে দূরে ঠেলে দেয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সে অবস্থানটিও খুব বেশি শক্তভাবে স্থায়ী ছিল না। আর তাই মোট তিনবার তিনি জাপান যাত্রা করেন যা মোট ছয়বার যাত্রায় রূপ নেয় যেহেতু ফেরার পথে প্রতিবারেই তিনি এই দ্বীপদেশটি স্পর্শ করে এসেছেন।
১৯১৯ সালে প্রকাশিত ‘জাপানযাত্রী’ বাংলা ভাষায় জাপান বিষয়ে একটি মাইফলক রচনা, যদিও এ প্রসঙ্গে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই গ্রন্থটির পরমাদরের পেছনের কবির বৈশ্বিক পরিচিতি ভূমিকা রেখেছিল সন্দেহ নেই। কেননা সত্যিকার অর্থে জাপানের ইতিহাসিক-ভৌগলিক-পৌরাণিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় ও শিক্ষাগত চিত্র সম্পর্কে সম্পর্কে জ্ঞানের প্রশ্নে মন্মথনাথ ঘোষের গ্রন্থত্রয় অধিকতর সুলিখিত ও তথ্যবহুল। ১৯১৬, ১৯২৪ ও ১৯২৯ সালে জাপান ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ যে সব বক্তৃতা দেন তার গ্রন্থরূপ ‘Talks in Japan’ ছাপার ব্যাপারে জীবদ্দশাতেই কবির ইচ্ছা থাকলেও তার প্রকাশ ঘটেছে সম্প্রতি – ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে।
প্রথম বার জাপান ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী ছিলেন কিশোর শিল্পী মুকুলচন্দ্র দে (১৮৯৫-১৯৮৯)। ভ্রমণকালের দিনলিপি ও লিখিত পত্রাবলী নিয়ে তাঁর গ্রন্থ ‘জাপান থেকে জোড়াসাঁকো’ (২০০৫) এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা ‘আমার কথা’ (১৯৯৫)-তেও জাপান ভ্রমণ সময়কাল স্থান পেয়েছে যথেষ্টভাবেই।
রবীন্দ্র-পরবর্তীকালে প্রধান যে দুজন বাঙালি লেখক জাপান ভ্রমণ করেন এবং দেশটির উপর গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাঁরা হলেন বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) এবং অন্নদাশংকর রায় (১৯০৯-২০০২)। অন্নদাশংকর রায়ের গ্রন্থ ‘জাপানে’ প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসুর ‘জাপানি জর্নাল’এর প্রকাশকাল ১৯৬২। ‘জাপানযাত্রী’, ‘জাপানে’ এবং ‘জাপানি জর্নাল’ যদি কোন পাঠক একই সাথে পড়া শুরু করেন, তাঁর নজরে আসবে গ্রন্থ তিনটির মধ্যেকার এক ধরনের সাযুজ্য।
বাংলা ভাষায় জাপান ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে গ্রন্থ রচনায় যে সকল সাহিত্যিক পরিব্রাজক অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের মধ্যে জাপানি অধ্যাপক বাংলাপ্রেমী কাজুও আজুমা (জন্ম ১৯৩১) অন্যতম। জাপান, রবীন্দ্রনাথ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তাঁর অন্তত চারটি গ্রন্থ রয়েছে। ‘প্রসঙ্গ: রবীন্দ্রনাথ ও জাপান’, ‘রবীন্দ্রনাথের টুকরো লেখা’, ‘জাপান ও রবীন্দ্রনাথ: শতবর্ষের বিনিময়’ এবং ‘জাপান, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য’ ছাড়াও তিনি অনুবাদ করেছেন কবিগুরুর ‘গোরা’, ‘চার অধ্যায়’, ‘মুক্তধারা’ – বাংলা থেকে জাপানিতে। অন্যদিকে জাপানি থেকে বাংলাতে অনুবাদ করেছেন কাম্পো আরাই-এর ‘ভারত ভ্রমণ দিনপঞ্জি’সহ আরো অনেক গ্রন্থ।
পশ্চিম বাংলা থেকে জাপান বিষয়ে প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: প্রভাষরঞ্জন দে’র ‘জাপান দেখে এলাম’, পবিত্র সরকারের ‘জাপানে কয়েকদিন’, ভূমিকায় উল্লিখিত মন্মথনাথ ঘোষের পুত্র কুমারেশ ঘোষের ‘জাপান-জাপানী’, নারায়ণ স্যানালের ‘জাপান থেকে ফিরে’, নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধায়ের ‘জাপান যেমন’, মুহম্মদ নূরুল ইসলামের ‘জাপানে যা দেখলাম’, আশুতোষ ভট্টাচার্যের ‘জাপানের আঙিনায়’, অজিত কুমার ঘোষের ‘সূর্যোদয়ের দেশে’, আশিষ সান্যালের ‘জাপান রবীন্দ্রনাথ এবং’ ইত্যাদি। এছাড়া ড. হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ‘জাপানের ইতিহাস’ দেশটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানতে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত। জাপান প্রবাসী আরেক অধ্যাপক সন্দীপ ঠাকুরের ‘পাথুরেঘাটা ঠাকুরবাড়ির গল্প’ গ্রন্থটির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জাপান সম্পর্কিত।
পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ অঞ্চলে জাপান বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ মোহাম্মদ মোদাব্বেরের (১৯০৮-১৯৮৪) ‘জাপান ঘুরে এলাম’। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে আজিমপুরের সবুজ লাইব্রেরি এটি প্রকাশ করে। ১৯৫৮ সালের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক শিশু কল্যাণ সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক সমাজ-কল্যাণ সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে লেখকের জাপান যাত্রার অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত এ গ্রন্থ। রবীন্দ্রসঙ্গীত পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী এ বক্তব্য উপস্থাপন করে ১৯৬৭-র ২২ জুন পাকিস্তান সরকার রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে সরকারের সে সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন মোহাম্মদ মোদাব্বের (দ্র. ‘বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান’, সম্পা: সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম, পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৯৭)। ১৯৭৬-৭৭ সালে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ‘আমার সোনার বাংলা’ পরিবর্তনের দাবীদার এ লেখক সাধারণ পাঠক কর্তৃক অগ্রাহ্য হলেও ভারত বিভাগ পরবর্তী পূর্ববাংলা অঞ্চলে তাঁর গ্রন্থটিই জাপান বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ।
পাকিস্তান আমলেই জাপান নিয়ে আরও যে একটি বাংলা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় তা হলো জোসেফাইন বাড ভন রচিত ‘জাপান’ গ্রন্থটির অনুবাদ। আহমদ ফজলুর রহমানের অনুবাদে এ গ্রন্থ ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরে ঢাকার নয়া দুনিয়া পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। জাপানের সামগ্রিক তথ্যাদি পরিবেশনে গ্রন্থটি একটি সফল প্রয়াস ছিল সন্দেহ নেই।
স্বাধীন বাংলাদেশে জাপান বিষয়ক গ্রন্থের রচনা ধীরগতির ছিল বলে ধারণা করা যায়। ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত অধ্যাপক মনসুর মুসার ‘জাপানের পথে’ সে ধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এছাড়া ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল আবদুল হাই শিকদারের ‘নিপ্পন নি সাগাগু’। ২০০৫ সালে প্রকাশিত ডা: আবদুস সাত্তারের ‘জাপান থেকে মেস্কিকো’র একটি অংশ জাপান নিয়ে তা শিরোনাম থেকেই স্পষ্ট। ২০০৭ সালে ফেব্রুয়ারিতে বেরিয়েছিল মুস্তাফা জামান আব্বাসীর সৃষ্টিশীল গ্রন্থ ‘জাপান’ যা পরবর্তী বছরেই দ্বিতীয় সংস্করণ লাভ করেছে। ইতোমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে কবি নির্মলেন্দু গুণের ‘পুনশ্চ জাপানযাত্রী’। ২০০৯ সালে সুফিয়া বেগমের ‘যেমন দেখেছি জাপান’ ছাড়াও প্রকাশিত হয়েছে প্রবীর বিকাশ সরকারের ‘জাপানের নদী নারী ফুল’ যেটিও লেখকের গবেষণাধর্মী ও ইতিহাস প্রিয় মননেরই ইঙ্গিত দেয়। যার আরেক বহিঃপ্রকাশ ছিল তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ‘জানা অজানা জাপান’। গ্রন্থটির ২৭০ পৃষ্ঠার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৮-এ এবং প্রায় একই কলেবরের দ্বিতীয় খণ্ডটির প্রকাশিত হয়েছে ফেব্র“য়ারি ২০০৯-এ। তাঁর খণ্ড দুটির দিকে মনোযোগ দিলে স্পষ্ট হয় যেমনভাবে প্রবীর বিকাশ সরকার বাংলাদেশ, ভারত বা বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির সাথে জাপানি সম্পর্কগুলোকে চিহ্নিত করেছেন, তেমনি তাঁর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে জাপান দেশ ও এর ভাষা সংস্কৃতির এমন কিছু বিষয় যা আমাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত না হলেও আগ্রহ সৃষ্টি করে।
আমাদের তথা বাংলাদেশ, অবিভক্ত বাংলা তথা ভারতবর্ষ এবং বাংলা ভাষার সাথে সম্পর্কযুক্ত যে প্রবন্ধগুলো প্রবীর বিকাশ উপস্থাপন করেছেন তার ভেতর যেমন রয়েছে ইতিহাস ও রাজনীতি তেমনি সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলোও গুরুত্বের সাথে উপস্থাপিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা যেতে পারে যে গবেষক প্রবীর বিকাশ সরকার জাপান সংশ্লিষ্টতায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুসন্ধান করছেন দীর্ঘদিন যার ছিঁটেফোটা সাম্প্রতিক ঈদ সংখ্যাগুলোতেও স্পষ্ট হয়েছে। বিশাল কলেবরে জাপান প্রাসঙ্গিকতায় রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক তাঁর এ গবেষণা গ্রন্থ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হবে এমন প্রত্যাশা করতে বর্তমান আলোচক দ্বিধান্বিত নন।
জানা অজানা জাপান গ্রন্থে সাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলোর তালিকার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। “দি বুক অব টী’ ও ‘গীতাঞ্জলি’: শতবর্ষের প্রাপ্তি’,‘বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জাপানি অনুরাগী, ‘অধ্যাপক কাজুও আজুমা এবং বাংলাদেশ’ এবং ‘ বাংলা জাপান সম্পর্কের প্রাণপুরুষ তেনশিন’। সতর্ক পাঠক খেয়াল করবেন উপর্যুক্ত চারটি প্রবন্ধ প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত তা সে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে ভাবেই হোক না কেন। এবং বাংলা সাহিত্য তথা রবীন্দ্রনাথ প্রেমী যে কোন পাঠকই লাভ করবেন নতুন জ্ঞানের অদ্ভুত এক আস্বাদ। সব কটি প্রবন্ধই যেমন ভালোলাগার উপলব্ধি জাগায় মনে, তেমনি ঋদ্ধ বোধ করার মত একটি আবেগও তৈরি করে।
জাপানি দার্শনিক ওকাকুরা তেনশিন (১৮৬২-১৯১৩) ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এর সংযোগের ভেতর দিয়ে জাপান-বাংলা সাহিত্যিক-দার্শনিক যোগাযোগের মাইলফলক সূচিত হয়েছিল। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত তেনশিনের গ্রন্থ ‘দি বুক অব টি’ এক এশিয়ার দার্শনিক ভিত্তি। জাপানে বহুল প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী চাদৌ বা চা উৎসব নিয়ে রচিত সে গ্রন্থ সম্পর্কে এর বাংলা অনুবাদক সুদীপ্ত চক্রবর্তী লিখেছেন:
‘দরদি প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত কাকুজো ওকাকুরা আমেরিকায় বসে যে-বইটি লেখেন তার স্বল্প পরিসরে বিধৃত রয়েছে গভীর ঐশ্বর্য। পাশ্চাত্য জীবনের পল্লবিত তেজ আর উচ্চকিত প্রদর্শনীর নিজস্ব শৈলীর মধ্যে বসে প্রাচ্যের প্রাচীনে সম্বৃত-গম্ভীর দর্শনের ধারাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন লেখক। তাঁর রচনায় মিশে আছে ইতিহাসবোধ, প্রজ্ঞা, শিল্পচেতনা, দেশপ্রেম আর আমাদের অধুনাতন সামূহিক চটুলতার প্রতি এক অভিমান। এ বইয়ে শিল্প, সমাজ আর মানুষের ইতিহাস একাকার হয়ে গেছে দার্শনিক চিন্তার আবহে। ইতিহাসের বন্ধ দরজা খুলে মরমি লেখক আমাদের দেখিয়েছেন কুয়াশাঘেরা এক রহস্যময় সুন্দর উপত্যকায় ছড়ানো মাণিক্যের চমক, ফুলের সৌরভ আর সর্বোপরি সেই স্বাদ যা এক সত্যিকার সোনার কাঠি।” (চা-চরিত, মনফকিরা, কলকাতা, ২০০৬, পৃ ৮)
জানা অজানা জাপান গ্রন্থে প্রবীর বিকাশ সরকার জানিয়েছেন ১৯০২ সালে প্রথমবারের মত ভারত ভ্রমণকালেই তেনশিনের সাথে যোগাযোগ ও নৈকট্য ঘটেছিল বাঙালি জাতির তৎকালীন অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবীদের যাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম।
যদিও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের প্রথমবার জাপান ভ্রমণের পূর্বেই তেনশিনের মৃত্যু হয় এবং ১৯২৪ সালে তিনি তেনশিনের ‘এশিয়া ইজ ওয়ান’ দর্শনের বিরোধিতাও করেন, সম্ভবত এ কারণে যে রবীন্দ্রনাথ ততদিনে ‘এক এশিয়া’র পরিবর্তে ‘এক বিশ্ব’ দর্শনে নিজেকে উপনীত করেছেন। তেনশিনের সাথে বাঙালি মহিলা কবি প্রিয়ম্বদা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৭১-১৯৩৫) যে প্রেম সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাও জানিয়েছেন প্রবীর বিকাশ (প্রথম খণ্ড, পৃ ১৭)। ১৯১২ সালে কলকাতায় তেনশিনের দ্বিতীয়বার ভ্রমণকালে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে, যা পরবর্তীতে পত্রপ্রেমে রূপ নিয়েছিল। জাপানের গেইশা রমনীদের জীবন নিয়ে প্রিয়ম্বদা রচনা করেন ‘রেণুকা’ (দ্র. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, ১ম খণ্ড, কলকাতা, সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৪)
১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীতে জাপান থেকে সত্য শিরোনামে মাসিক ট্যাবলয়েড একটি কাগজের ২২টি সংখ্যা বের হয়েছিল যে তথ্য রীতিমত চমক সৃষ্টিকারী। প্রবীর বিকাশ সে সংখ্যাগুলোর প্রধান সূচি শিরোনাম উৎকলন করেছেন পাঠকের জন্য (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৬১)। রবীন্দ্র-আগ্রহী বা জাপানে বাংলা সম্পর্কে আগ্রহী যে কোন পাঠকের জন্য এ সূচি রীতিমত উদ্দীপক। রবীন্দ্রনাথ বারবার জাপান গেছেন, সরকার প্রধান থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত স্তরে তাঁর সংযোগ ঘটেছে সত্য, কিন্তু তাঁকে নিয়ে শতবর্ষ উদ্যাপনে এমন যজ্ঞজ্ঞান বিশেষ করে বিদেশের মাটিতে বোধ হয় বিশ্বাসে চাক্ষুস প্রত্যক্ষতা দাবী করে। এশিয়ার প্রথম নোবেল বিজয়ী হিসেবে জাপানে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যাত্রা পুরো জাপান জাতির জন্য যেমন ছিল একটি উৎসবমত ব্যাপার তেমনি প্রথম যাত্রাতেই জাপানের বিশ্বনীতি-রাজনীতি-রণনীতিকে তাঁর বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্ত করতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ যে বিমুখতার মুখোমুখি হয়েছিলেন তা অপসারিত হতে সময় লেগেছিল অনেক।
জাপানে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসহ সামগ্রিক চিত্রটি পেতে প্রবীর বিকাশের গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান। হয়তো এ কথা বলা অত্যক্তি হবে না যে জানা অজানা জাপান এ বিষয়ক অগ্রগণ্য একটি প্রকাশ। যাঁরা বুদ্ধদেব বসুর জাপানি জর্নাল বা অন্নদাশংকর রায়ের জাপানে পড়েছেন তাদেরও স্মরণ থাকতে পারে যে জাপানযাত্রীর সমগোত্রীয় বই সে দুটো। ভ্রমণ অভিজ্ঞতা থেকে লেখা ভ্রমণ কাহিনী। অন্যদিকে ভ্রমণকৃত দেশ বিষয়ে ইতিহাসিক ও অন্যান্য আলোকে তথ্যসমৃদ্ধতায় বিশ্লেষণের যে প্রয়াস সুরেশচন্দ্র বা মন্মথনাথ করেছিলেন প্রবীর বিকাশের জানা অজানা জাপান তেমন ঘরানার।
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে আগ্রহী জাপানিদের বিষয়ও প্রবীর বিকাশ পরিস্ফুট করেছেন অনেক বি¯তৃত করে, ঋদ্ধতার আলোকে। তেমন জাপানি অগ্রগণ্য পুরুষ হলেন কাজুমা আজুমা। রবীন্দ্র রচনার জাপানি অনুবাদ, জাপানে রবীন্দ্র সাহিত্য প্রসার ইত্যাকার সকল কাজে তাঁর নমস্য ভূমিকা। জাপান-বাংলা প্রাসঙ্গিকতায় পথিকৃত সে জাপানির উত্তরসূরি হিসেবে প্রবীর বিকাশকে চিহ্নিত করা যায় সহজেই। আজুমার গ্রন্থের অনেক বিষয়ই প্রবীর বিকাশের গ্রন্থেরও বিষয়, তবে প্রবীর বিকাশ প্রথমবারের মত আজুমা লিখিত প্রসঙ্গগুলোকে অনেক পরিশীলিত ও সামগ্রিকতায় উপস্থাপন করেছেন। গভীর অনুধ্যান এবং একনিষ্ঠতার সাথে সময় ও পরিশ্রমকে যুক্ত করতে পেরেছেন বলেই প্রবীর বিকাশ সম্ভব করতে চলেছেন জাপানে রবীন্দ্রনাথ প্রাসঙ্গিকতায় সহস্রাধিক পৃষ্ঠার একটি মূল্যবান গ্রন্থ। দেশের পত্রপত্রিকায়, বিশেষ করে ঈদসংখ্যাগুলোতে এবং অনলাইনে বিশেষ করে তাঁর সে সংক্রান্ত প্রবন্ধটির প্রকাশ আগ্রহী পাঠকের দৃষ্টি কেড়েছে বলে বর্তমান আলোচকের বিশ্বাস।
সাহিত্য ব্যতিরেকে জাপান-বাংলা প্রসঙ্গে যে সকল প্রবন্ধ গ্রন্থে সন্নিবেশিত সেগুলো হল ‘ইচিনোসে তাইজোর চোখে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ’, ‘মাসাআকি তানাকার দৃষ্টিতে শেখ মুজিব’, ‘জাপানিদের পূর্বপুরুষরা ভারতীয়!’, ‘বিপ্লবী রাসবিহারী বসু এবং ভারতের স্বাধীনতা’, ‘নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং জাপান’, ‘জাপানে শান্তির দূত বিচারপতি ড. রাধাবিনোদ পাল’, ‘ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রিয় এক জাপানি নারী’, “সোকা’; জাপান-বাংলার অন্যরকম সেতু’, ‘বাংলাদেশে মৌলবাদী: উদ্বিগ্ন জাপানি সমাজ’, ‘জাপানে ভারতীয় ‘কারি’র ইতিহাস’ ইত্যাদি। বাঙালি সমাজের কাছে প্রিয় নাম সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে যে কোন রচনাই এখনো আনন্দের আধার। সে রচনাতে জাপান সংসর্গে সুভাষচন্দ্রকে ভাবতে রোমহর্ষ হয়। প্রবীর বিকাশ উপস্থাপন করেছেন সুভাষচন্দ্রের জাপানি প্রেক্ষাপট, তাঁর জাপান গমন, অবস্থান , মৃত্যু সবই। এমনকি রেনকোজি বৌদ্ধ মন্দিরে সুভাষচন্দ্রের চিতাভস্মের সংরক্ষণ নিয়ে যে সন্দেহের প্রচার তারও বিশ্লেষণ লেখক করেছেন। সুসংহতভাবে প্রবন্ধকারে সে সকল তথ্যের বিন্যাসে প্রবীর বিকাশ তাঁর মনন ও অনুসন্ধিৎসাকে সংমিশ্রণ করতে পেরেছেন বলেই এ সকল প্রবন্ধ হয়ে উঠেছে সুখকর। রাসবিহারী বসু বা রাধাবিনোদ পালকে নিয়েও লেখকের অনুসন্ধান পাঠকের ঔৎসুক্য বৃদ্ধিকারী।
পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার দুটি খণ্ডে এমন অনেক প্রসঙ্গ রয়েছে যেগুলো নিয়ে সাধারণ বাঙালি পাঠকের আগ্রহের সম্ভাবনা কম। ‘তোজো হিদেকি: জাপানের শেষ সামুরাই’, ‘অনুসরনীয় জাতীয়তাবাদী শিরাসু জিরো’, ‘অলৌকিক এক যুগের নাম শোওয়া’ ইত্যাদির কথা খুব সহজেই মনে আসে। গ্রন্থনাম ও বিষয় বিবেচনায় এগুলোকে অপ্রাসঙ্গিক অভিধা দেওয়া চলে না নিশ্চয়ই, কিন্তু আগ্রহ প্রশ্নে সেগুলোকে ‘অনাদরিত’র তালিকায় রাখতে দোষ নেই। ধারণা হয়, প্রবীর বিকাশ যখন জাপান-প্রাসঙ্গিকতায় প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন ক্রমে তাঁর সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং সবগুলোকে প্রথমে একটি খণ্ডে এবং পরেরগুলোকে দ্বিতীয় আর একটি খণ্ডে সন্নিবেশের চিন্তা লেখকের হয়েছিল।
মোট ৩৫টি প্রবন্ধের জানা অজানা জাপান কখনো কখনো দুষ্ট হয়েছে পৌনঃপুনিকতার কারণেও যার উৎসও খোঁজা যেতে পারে উপর্যুক্ত প্রসঙ্গটিতে। একটি গ্রন্থকল্পকে আগেভাগেই সচেতনায় না আনতে পারলে এটি এড়ানো প্রায় অসম্ভব এবং প্রবীর বিকাশ সরকারের জন্যেও সেটিই ঘটেছে। কিন্তু তারপরও নির্দ্বিধচিত্তে বলতে চাই জাপান-প্রাসঙ্গিকতায় বাংলা ভাষায় যত বই রচিত হযেছে স্বাভাবিক কারণেই সেগুলোর অধিকাংশই ভ্রমণকাহিনী – কখনো সাধারণ বিবরণে পূর্ণ, কখনো বিবরণকে ঋদ্ধ করেছে সে দেশের ঐতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির বিষয়াদি। জানা অজানা জাপান জাপান ভ্রমণ বিবরণ ব্যাতিরেকে জাপানের প্রসঙ্গাদি নিয়ে রচিত।
আলোচনা শেষ করার আগে জাপান-প্রাসঙ্গিকতায় একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা জানাতে চাই। ইউনেস্কো কর্তৃক আয়োজিত আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপের প্লাটফর্ম ‘মনডিয়ালোগো’তে ২০০৮ সালে জাপানের কোবে ফুকিয়াই মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের সাথে আমার তৎকালীন কর্মস্থল বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ রাইফেলস্ কলেজের শিক্ষার্থীদের যৌথ উদ্যোগে একটি দ্বিভাষী (ইংরেজি ও জাপানি) হাতে বাঁধানো বই প্রকাশ করা হয় আমাদের শহীদ দিবস নিয়ে। সে গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে পিলখানা চত্বরে আমার আহ্বানে এসেছিলেন তৎকালীন জাপানি রাষ্ট্রদূত মাসাইউকি ইনোওয়ে। প্রজেক্ট চলাকালে ছাত্রছাত্রীদের জাপানযাত্রী পড়ানোর সূত্রেই গ্রন্থটির পনুঃপাঠ ঘটে আমার। জুন-জুলাই নাগাদ যোগাযোগ ঘটে প্রবীর বিকাশ সরকারের সাথে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে। বাংলাদেশে এলে তিনি তাঁর জানা অজানা জাপান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি আমাকে উপহার দেন যার ফলে জাপান বিষয়ক, বিশেষ করে বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমার অনুসন্ধিৎসা বাড়তে থাকে। সে সময় যোগাযোগ ঘটে ঋদ্ধ পাঠক সুকান্ত সৈকতের সাথে যিনি শর্তহীনভাবে তাঁর গ্রন্থাগার থেকে বই যোগান দিয়ে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তেমন সময়েই মাগুরার বেরইল কলেজের অধ্যক্ষ আমার পিতৃপ্রতিম কাজী ফিরোজের সহযোগিতায় হাতে পাই জাপান বিষয়ক দুর্লভ একটি গ্রন্থ। আর এভাবেই বাংলা ভাষায় জাপান বিষয়টি আমার আগ্রহে পল্লবিত হতে থাকে। প্রবীর বিকাশের বইটি আমার সে-পল্লবায়নে অসামান্য চালিকাশক্তির কাজ করেছে। সেজন্য, ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর প্রতি ঋণী।
প্রবীর বিকাশ সরকারের জাপানে অবস্থিতি ২৫ বছরের বেশি। উচ্চতর শিক্ষা, সংসার সবকিছুই ক্রমে ক্রমে সেখানে দৃঢ় প্রোথিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষা সাহিত্যে অনুরাগের কারণেই ইতিহাসের ছাত্র প্রবীর বিকাশের পরিচয় ক্রমপ্রকাশিত। সেই কবে ছড়া লিখেছেন, জাপান থেকে বের করেছেন বাংলা ভাষার পত্রিকা মানচিত্র, লিখেছেন উপন্যাস তালা, অভিজিৎ, প্রচ্ছায়া, অতিথি ইত্যাদি। কিন্তু তাঁর সে সকল পরিচয়কে ছাড়িয়ে উজ্জ্বলতর তাঁর প্রাবন্ধিক অভিধাটি। গভীর অভিনিবেশে প্রবাসকালে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান পুরুষ রবীন্দ্রনাথকে যেমন অনুপুঙ্খতায় চিত্রায়ণ করে চলেছেন তেমনি দুই জাতি বাঙালি-জাপানির অনালোকিত ইতিহাসকে আলোকদান করে জাতির কাছে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে চলেছেন সন্দেহ নেই।